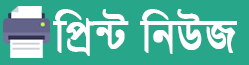
রবীন্দ্রনাথের কথা চিন্তা করলেই আমাদের মানসপটে শ্বেত-শুভ্র লম্বা চুল দাড়িবিশিষ্ট একজনের ছবি আসে। মনে হয়, তিনি সারা দিন কবিতা ও সাহিত্য সাধনাতেই মগ্ন ছিলেন, যেন জগৎ-সংসারের অন্য কোনো বিষয় তাদের মাথায় আসে না—এ ধরনের চিত্রের সঙ্গে পল্লি সংস্কারক রবীন্দ্রনাথের মিল নেই। প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনো খেয়ালি উদাসীন মানুষ ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রকৃত সমাজ সংস্কারক। তিনি বুঝতেন, সাধারণ জনগোষ্ঠীর উন্নতি ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন বা স্বাধীনতার কোনো বাস্তব মূল্য নেই। অন্য নেতারা ভাগবাঁটোয়ারায় ব্যস্ত থাকলেও তিনি সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন। এভাবেই পরিচিত কবি রবীন্দ্রনাথকে আমরা নতুন রূপে পাই।
ছেলে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘কিছুদিন পর বাবা দেখলেন প্রজারা ঋণমুক্ত না হলে উন্নতি করতে পারবে না। কৃষি বা শিল্পের জন্য দরকারি মূলধন তাদের হাতে থাকবে না। তাই বাবা পতিসরে একটি ব্যাংক খুললেন। কয়েকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যাংকের কাজ শুরু হলো। পরে বাবা যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, এক লাখের ওপর টাকাই কৃষি ব্যাংকের কাজে দিলেন। কৃষি ব্যাংক প্রজাদের অনেক উপকারে এল—কয়েক বছরের মধ্যে তারা মহাজনদের দেনা শোধ করতে পারল।’
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাজ কিন্তু শুধুমাত্র পতিসরের উন্নয়ন নয়, বরং আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থার মডেল স্থাপন। আমরা দেশে ও বিদেশে নানা শিক্ষাব্যবস্থার মডেল খুঁজি, কিন্তু চোখের সামনেই বিদ্যমান শান্তিনিকেতন। শিক্ষাক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদান নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয় না। কারণ তার সাহিত্য জগতের দ্যুতি এতটাই প্রখর যে, আশপাশের অন্যান্য বিষয় সহজে নজরে আসে না।
দেশ-রাষ্ট্র-ধর্ম-জাতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ উদারনৈতিক চেতনার অধিকারী ছিলেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ১৯১৪ সালে তিনি কোনো এক ইংরেজ পাঠিকাকে লিখেছেন,
‘I do not belong to any religious sect nor do I subscribe to any particular Creed. That I know that the moment my God has created me he has made himself mine.’
এই আন্তর্জাতিক উদারচেতনা শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি লালন করতেন। অল্প বয়সেই তিনি শিক্ষাব্যবস্থার অসাড়তা ধরতে পেরেছিলেন। ষোলো বছর বয়সে ‘ভারতী’ পত্রিকায় লিখেছেন—
বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টি ছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কিছু বুলি এবং ইতিহাসের ঘটনা মুখস্থ করিতে পারলেও, রুচি উন্নতি বা স্বাধীন চিন্তাশীল হতে শিখতে পারে না।
এ চিন্তা পরিণত বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল ‘শান্তিনিকেতন’ ও ‘শ্রীনিকেতন’-এ। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুকে ১৯০১ সালে লিখেছেন,
শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় খুলতে বিশেষ চেষ্টা করছি। সেখানে প্রাচীনকালের গুরুগৃহের নিয়ম অনুসরণ করা হবে। এখনকার কালের বিদ্যা ও প্রাচীন কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যাবে না। ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম’ নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ডিগ্রি বা চাকরির সামাজিক গুরুত্ব থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তা গৌণ স্থান দিয়েছেন।
তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যা পাচ্ছে, তা ক্লাসের জিনিস নয়—প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। বৃষ্টিতে ছুটে বেড়ানো, জ্যোৎস্না রাত্রিতে আনন্দ, গাছে চড়ে পড়া—এসব জীবনকে সার্থক করে।’
শ্রীনিকেতনে তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেন। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি আশাহত হন। ১৯৩৯ সালে শান্তিনিকেতনের শিক্ষক তেজেসচন্দ্র সেনকে লিখেছেন,
‘আমি দুঃখ পাই—প্রত্যহ দেখি, আশ্রমের প্রাণ সেবা পৌঁছায় না। আশ্রম শুধু স্কুল নয়, জীবনচর্চার স্থান।’
রবীন্দ্রনাথ শোষিত জনগণের পাশে দাঁড়ান। মহাজনদের কাছ থেকে কৃষকদের ঋণ মুক্ত করতে পতিসর কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেন। নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকাও কৃষকদের সুবিধার্থে ব্যাংকে জমা রাখেন।